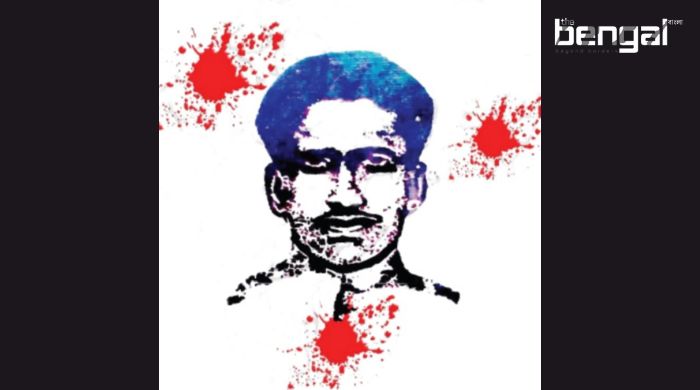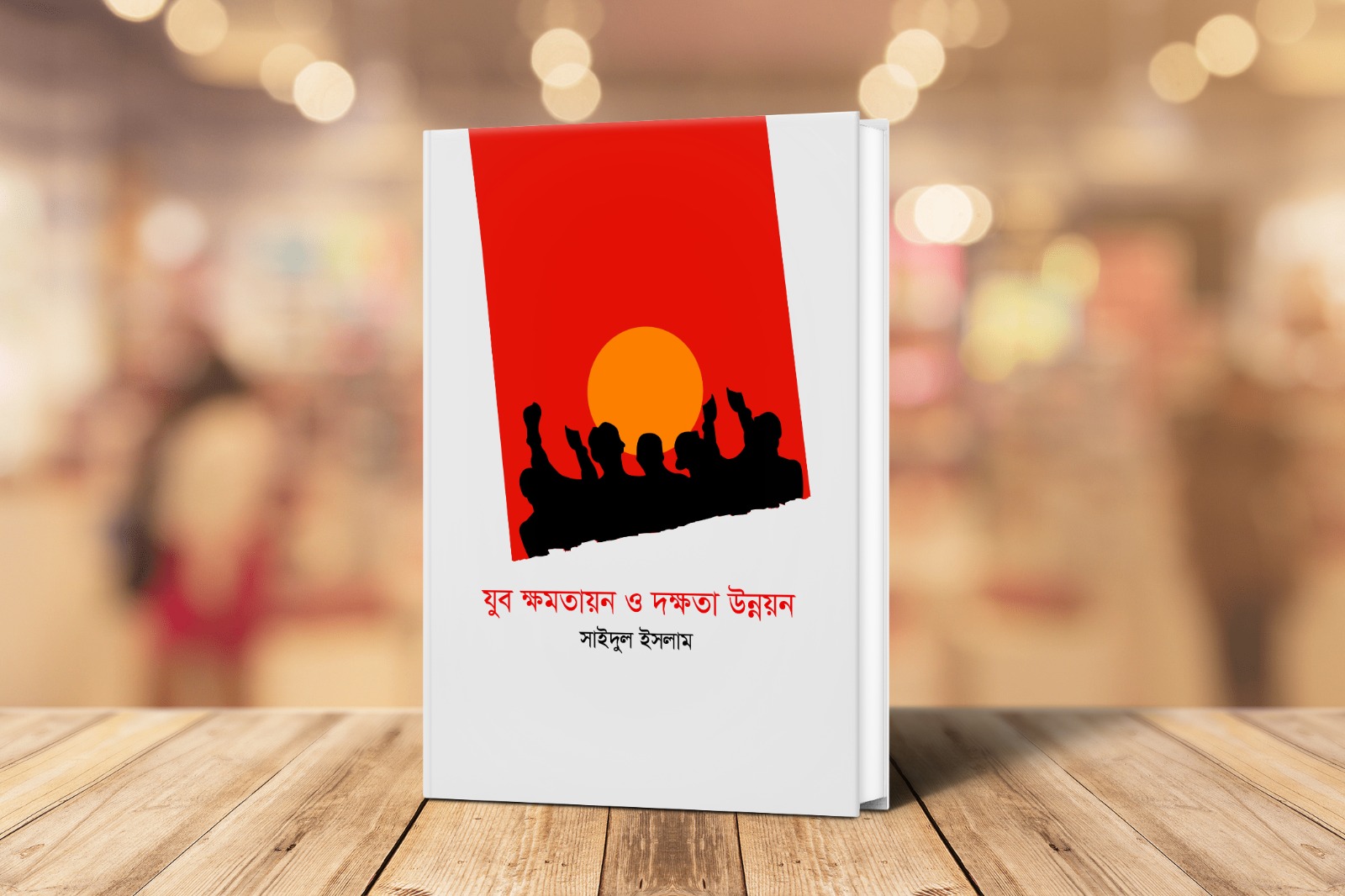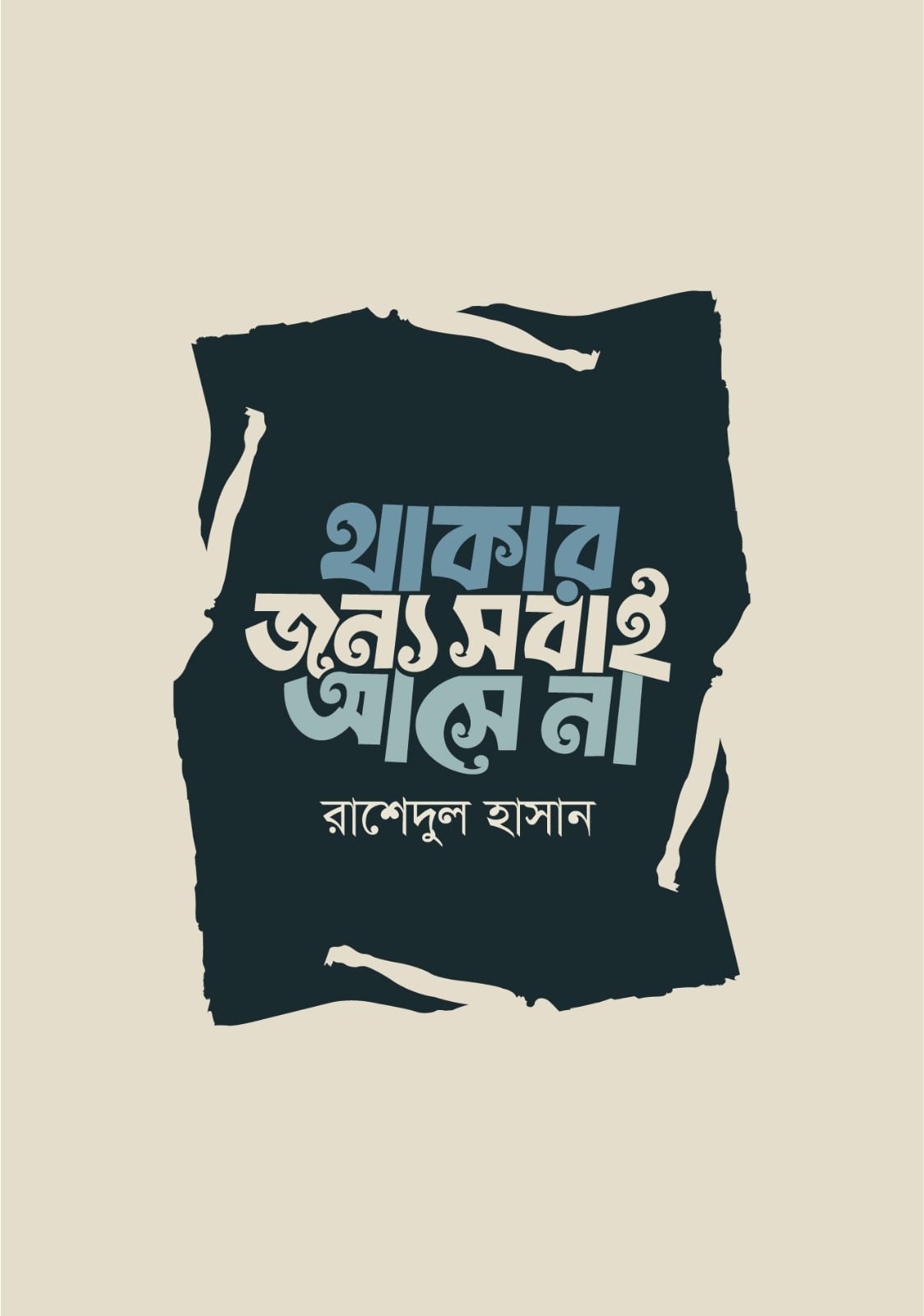ঢাকা: তিস্তা নদী বাংলাদেশের জন্য কেবল একটি জলাধার নয়, এটি কৃষি, বাস্তুতন্ত্র, অর্থনীতি এবং জাতীয় নিরাপত্তার সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। দেশের উত্তরাঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা এ নদীর পানির ওপর নির্ভরশীল, বিশেষ করে শুষ্ক মৌসুমে।
কিন্তু বাস্তবতা হলো, ভারত একতরফাভাবে তিস্তার উজানে বাঁধ দিয়ে পানি নিয়ন্ত্রণ করছে, ফলে বাংলাদেশ শুষ্ক মৌসুমে পানির অভাবে এবং বর্ষায় অতিরিক্ত পানির চাপে ভয়াবহ সংকটে পড়ে। প্রায় চার দশক ধরে চলা আলোচনা সত্ত্বেও তিস্তা নদীর পানি বণ্টন চুক্তি ভারতের প্রতিশ্রুতির বাইরে আর কিছুই হয়নি।
২০১১ সালে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের ঢাকা সফরে একটি চুক্তির খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছিল, যেখানে ৩৭.৫ শতাংশ পানি বাংলাদেশ এবং ৪২.৫ শতাংশ ভারত পাবে বলে বলা হয়েছিল।
কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপত্তির কারণে এই চুক্তি বাস্তবায়ন হয়নি। এরপর থেকে ভারত বারবার প্রতিশ্রুতি দিলেও বাস্তবে কোনো অগ্রগতি হয়নি। বরং, ভারতের একতরফা পানি প্রত্যাহারের ফলে বাংলাদেশ দিন দিন ভয়াবহ জলসংকটে পড়ছে।
এই বাস্তবতায় বাংলাদেশ সরকার তিস্তা মহাপ্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বিকল্প পথ খুঁজতে শুরু করেছে, যার অংশ হিসেবে চীনের সঙ্গে একটি নতুন চুক্তির আলোচনা চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। চীনের রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান পাওয়ার চায়না তিস্তা নদী ব্যবস্থাপনায় ৮৫৩ মিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ প্রস্তাব দিয়েছে, যা বাংলাদেশের জন্য একটি বড় সুযোগ।
এই প্রকল্পের মাধ্যমে নদীর দুই পাড়ে আধুনিক বাঁধ নির্মাণ, খননকাজ, জলাধার তৈরি, সেচব্যবস্থা উন্নয়ন, সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন এবং পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এতে শুধু পানির প্রবাহ নিয়ন্ত্রণই হবে না, বরং নদীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নও ত্বরান্বিত হবে।
কিন্তু এই চুক্তি নিয়ে ভারত উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। তাদের মতে, চীনের উপস্থিতি ভারতের জন্য কৌশলগত ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। ভারত মনে করে, এই অঞ্চলে চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব দক্ষিণ এশিয়ার ভূরাজনৈতিক ভারসাম্যকে পরিবর্তন করতে পারে।
তবে বাংলাদেশ সরকার এই প্রকল্পকে সম্পূর্ণভাবে একটি অর্থনৈতিক উদ্যোগ হিসেবে দেখছে এবং জাতীয় স্বার্থে চীনকে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
তবে প্রশ্ন থেকে যায়— এটি কি শুধুই একটি অবকাঠামোগত প্রকল্প, নাকি এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের নতুন মেরুকরণ ঘটবে? একদিকে ভারত দীর্ঘদিন ধরে তিস্তা নিয়ে গড়িমসি করছে, অন্যদিকে বাংলাদেশ তার নিজস্ব স্বার্থ রক্ষার জন্য একটি বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।
চীন যদি এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করে, তাহলে এটি ভারতের জন্য একটি কৌশলগত বার্তা হতে পারে যে, বাংলাদেশ এখন আর একপাক্ষিক প্রতিশ্রুতির ওপর নির্ভর করবে না।
তিস্তা মহাপ্রকল্পের বাস্তবায়ন শুধু পানি সংকট নিরসন করবে না, এটি বাংলাদেশের সার্বভৌম সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতার প্রতিফলনও হবে। এটি প্রমাণ করবে যে, বাংলাদেশ নিজের স্বার্থ রক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতাকে কৌশলগতভাবে ব্যবহার করতে সক্ষম।
সুতরাং, তিস্তা নদী নিয়ে ভারতের একচেটিয়া মনোভাবের দিন হয়তো শেষ হতে চলেছে। বাংলাদেশ এবার নিজস্ব স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে এবং প্রয়োজনে বিকল্প পথ বেছে নিচ্ছে। এই পরিবর্তন শুধু জলবণ্টন চুক্তির ক্ষেত্রে নয়, আঞ্চলিক ভূরাজনৈতিক সমীকরণেও একটি নতুন মাত্রা যোগ করবে।

 মো: আবদুস সালাম ফরায়জী
মো: আবদুস সালাম ফরায়জী