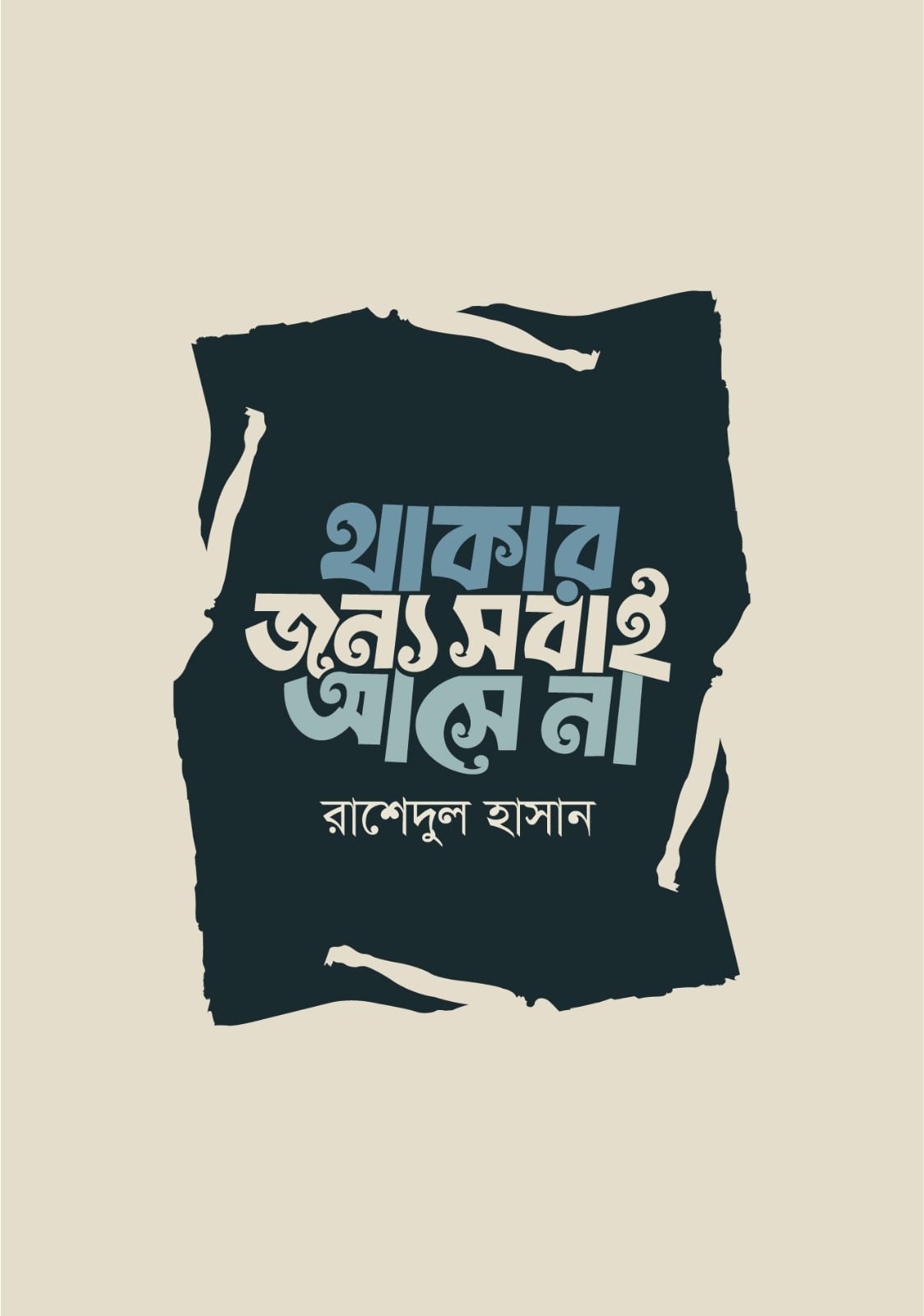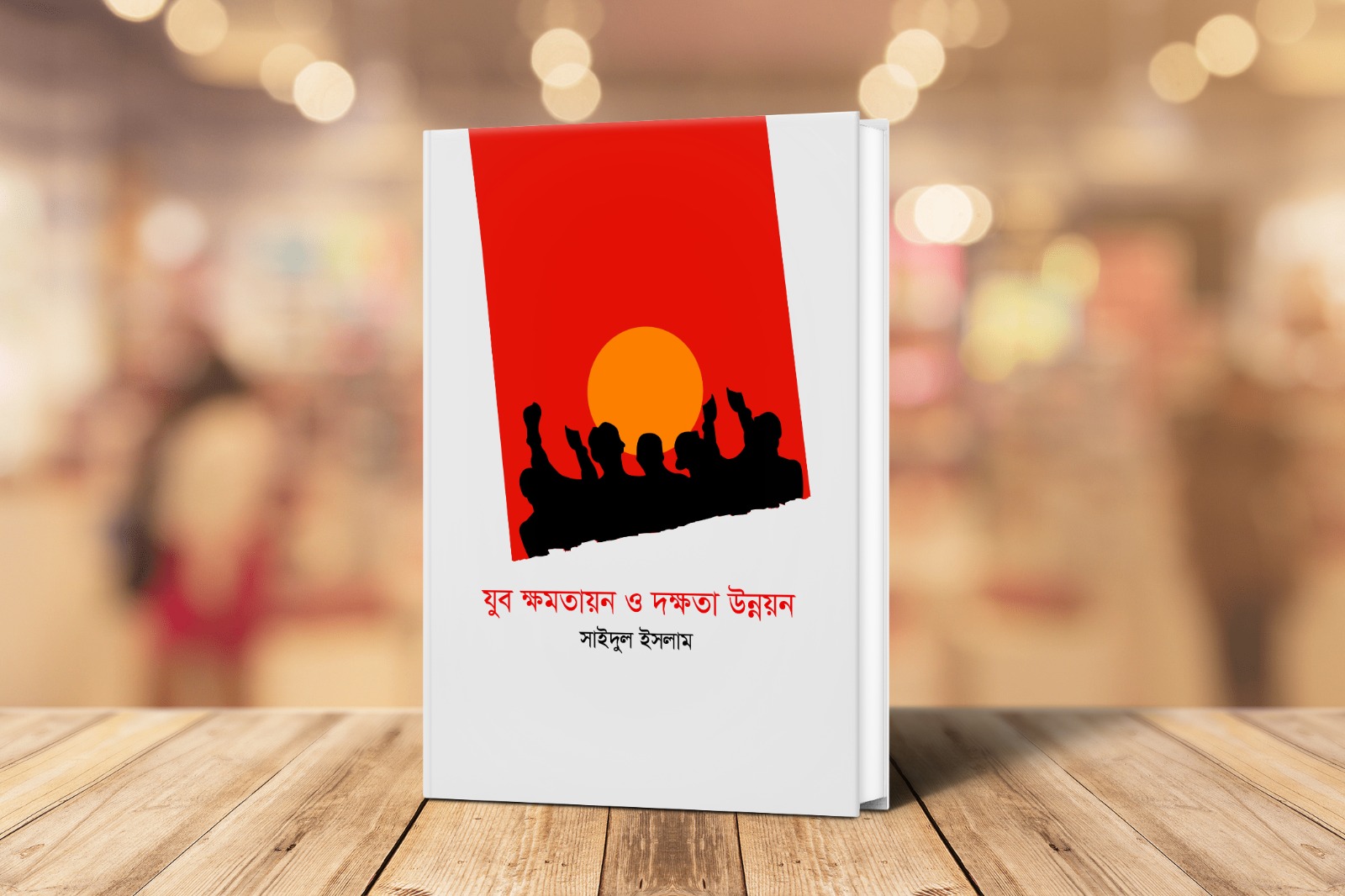এস এম সৈকত
বাংলাদেশে যৌন সহিংসতার শিকারদের জন্য ন্যায়বিচার যেন এক দূরহ স্বপ্ন । ধর্ষণের মামলা জমতে থাকে, বিচার প্রক্রিয়া বছরের পর বছর গড়ায়, আর অপরাধীরা মুক্ত ঘুরে বেড়ায়, কারণ আমাদের বিচারব্যবস্থা তাদের জন্য কার্যকর শাস্তির নিশ্চয়তা দিতে ব্যর্থ হচ্ছে। যখন আইন তার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়, তখন আরও একটি ভয়ংকর প্রবণতা বাড়তে থাকে—জনতার বিচার বা ‘মব লিঞ্চিং’। হতাশ ও ক্ষুব্ধ জনগণ নিজেরাই আইন হাতে তুলে নিচ্ছে, পুলিশের হেফাজত থাকা অবস্থায়ও অভিযুক্তদের প্রকাশ্যে শাস্তি দিচ্ছে। কিন্তু এই অবাধ সহিংসতা কি প্রকৃতপক্ষে কাউকে নিরাপদ করছে? নাকি আমরা কেবল এক ধরনের অরাজকতার বদলে আরেকটি নতুন বিশৃঙ্খলাকে স্বীকৃতি দিচ্ছি?
সম্প্রতি মাগুরায় আট বছর বয়সী এক শিশুকে ধর্ষণের ঘটনা আমাদের বিচারব্যবস্থার করুণ চিত্র তুলে ধরেছে। অভিযুক্ত—তার বোনের শ্বশুর, যে এর আগেও একই ধরনের অপরাধে জড়িত ছিলো, কিন্তু কোনো শাস্তির মুখোমুখি হয়নি। ফলে, নতুন শিকার তার সর্বশেষ নৃশংসতার শিকার হলো এবং এখন জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে। এটি কোনো ব্যতিক্রম নয়; এটি আমাদের সমাজের বাস্তব চিত্র। যারা ন্যায়বিচার চায়, তাদের দীর্ঘ ও অপমানজনক একটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। পুলিশের গাফিলতি, প্রশাসনিক জটিলতা, এবং সামাজিক লজ্জার ভয়ে অনেক ভুক্তভোগী নীরব থাকে। আর যারা সাহস করে অভিযোগ জানায়, তাদের জন্য অপেক্ষা করে বছরের পর বছর চলা বিচার প্রক্রিয়া, যা অনেক সময় ভিকটিমের জীবদ্দশায় শেষ হয় না।
ফলে, একটি বিপজ্জনক প্রবণতা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে। যখন আইনি পথ ব্যর্থ হয়, তখন জনগণ নিজেরাই আইন হাতে তুলে নেয়। এক ঘটনায়, পুলিশের হেফাজতে থাকা ধর্ষণে অভিযুক্ত এক ব্যক্তিকে আদালত চত্বরেই রাগান্বিত জনতার রোষানলে পড়তে দেখা গেছে। আরেকটি ঘটনায়, ধর্ষণের মামলায় অভিযুক্তের পক্ষে আদালতে দাঁড়ানোর জন্য এক আইনজীবীকে আদালতের বাইরে মারধর করা হয়। অনেকের কাছে এই ঘটনাগুলো বিচার পাওয়ার একটি মাধ্যম বলে মনে হতে পারে অথবা কেউ কেউ বলছেন এটি একটি ব্যর্থ বিচারব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিক্রিয়া। কিন্তু বাস্তবে, এই ধরনের মব লিঞ্চিং সমাজের আইনি কাঠামোকে দুর্বল করে দেয়। যখন মানুষ বিশ্বাস করতে শুরু করে যে আইন তাদের রক্ষা করতে পারবে না, তখন তারা আইন মেনে চলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না। এর পরিণতিতে আরও বিশৃঙ্খলা, আরও সহিংসতা, এবং আরও বেশি ঝুঁকির মধ্যে পড়ছে শিশু ও নারীরা।
জনতার বিচার যৌন সহিংসতাকে দমন করে না; বরং এটি ভয়ের সংস্কৃতিকে আরও গভীর করে তোলে। ভুক্তভোগীরা হয়তো অভিযোগ জানাতেই দ্বিধান্বিত হবে, কারণ তারা জানে যে এতে প্রকৃত বিচার না হয়ে আরও বড় সহিংসতার জন্ম হতে পারে। কিছু ক্ষেত্রে, ধর্ষণের অভিযোগ জানানো নারীদের সামাজিকভাবে লাঞ্ছিত হতে হয়, তাদের “পরিবারের সম্মান নষ্ট করার” অভিযোগে দোষারোপ করা হয়, এমনকি তারা প্রতিশোধপরায়ণতার শিকার হচ্ছেন। অপরাধীরাও শিখে যায় যে আইনকে ফাঁকি দেওয়া মানেই শাস্তি এড়ানো নয়; বরং তাদের অপেক্ষা করছে এক অনিশ্চিত জনতার প্রতিশোধ, যেখানে অপরাধের প্রমাণ নয়, বরং জনতার ক্রোধই বিচার নির্ধারণ করবে। এ অবস্থায় তারা সংগঠিত হয়ে নানান গোষ্ঠী বা দলের ছত্রছায়ায় অপরাধ সংঘটন করার প্রবণতা সৃষ্টি করে। আবার মব জাস্টিসের মুখে পূর্বশত্রুতার জেরে কাউকে ফাঁসানোর মতন ঘটনাকেও উড়িয়ে দেয়া যাবে না।
একটি দেশের বিচারব্যবস্থা কি এইভাবে চলতে পারে? আমরা যদি এই চক্র ভাঙতে চাই, তাহলে আমাদের সমস্যার মূল উৎসেই সমাধান খুঁজতে হবে: আইনি সংস্কার। ধর্ষণবিরোধী আইন শুধু কাগজে নয়, বাস্তবেও কার্যকর করতে হবে। দ্রুত বিচার নিশ্চিত করতে হবে, যেন ভুক্তভোগীদের বছরের পর বছর অপেক্ষা করতে না হয়। পুলিশকে অবশ্যই লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার মামলাগুলো দ্রুত ও সংবেদনশীলতার সাথে পরিচালনা করতে প্রশিক্ষণ দিতে হবে, যেন কোনো অপরাধী অবহেলা বা দুর্নীতির কারণে মুক্ত হয়ে না যায়। এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, জনগণের বিচারব্যবস্থার প্রতি আস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে—কারণ যখন মানুষ আদালতের ওপর বিশ্বাস হারায়, তখন তারা নিজেরাই বিচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়, যার পরিণতি হয় আরও অরাজকতা ও প্রাণহানি।
এটি শুধুমাত্র অপরাধীদের শাস্তির বিষয় নয়; এটি সমাজকে রক্ষা করার বিষয়। যদি কোনো দেশে ন্যায়বিচার অনিশ্চিত হয়, যদি নারীরা প্রতিদিন আতঙ্কে জীবনযাপন করে, এবং যদি রাস্তায় জনতা নিজেই শাস্তি কার্যকর করতে শুরু করে, তাহলে সেই দেশ-সমাজ কার্যত সবক্ষেত্রেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। যৌন সহিংসতার সমাধান আরও সহিংসতা নয়; সমাধান হলো এমন একটি কার্যকর আইনি কাঠামো, যা ভুক্তভোগীদের কথা শোনে, অপরাধীদের কঠোরভাবে শাস্তি দেয়, এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে—জনতার ক্রোধের মাধ্যমে নয়, বরং আইন ও নীতির মাধ্যমে। ন্যায়বিচারের একমাত্র বিকল্প কেবলই ‘ন্যায়বিচার’।
লেখক- একজন মানবাধিকার কর্মী এবং সিরাক-বাংলাদেশ এর নির্বাহী পরিচালক।
ই-মেইল: shaikatsm@gmail.com